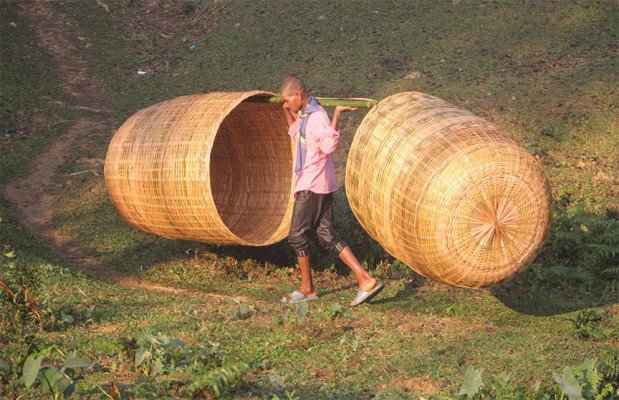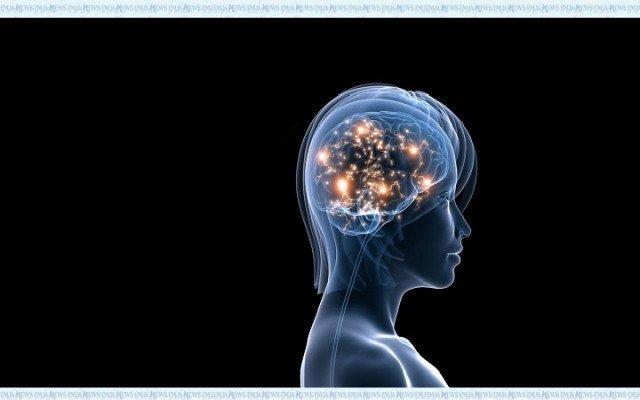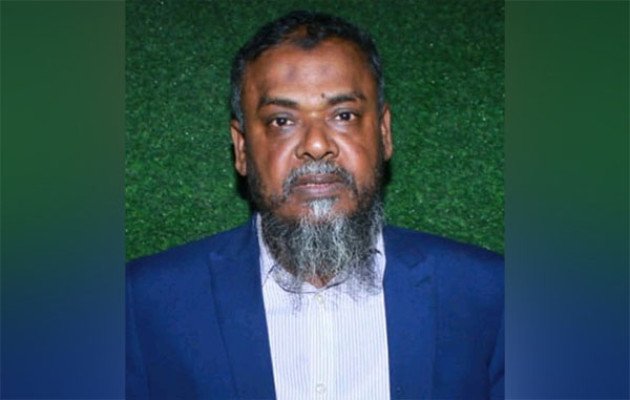ছবি- গুগল
২১ জুন বিশ্ব সংগীত দিবস। এই দিনে বিশ্বব্যাপী সঙ্গীতপ্রেমীরা কণ্ঠে, তালে, ছন্দে উদযাপন করেন মানবিক অনুভব ও সংস্কৃতির অন্যতম শক্তিশালী বাহন- সঙ্গীতকে। সঙ্গীত একদিকে যেমন বিনোদনের অনিবার্য অংশ, অন্যদিকে তা শিক্ষা, প্রতিবাদ, দর্শন ও মানবিকতারও অভিব্যক্তি।
বিশ্বজুড়ে আজ সুর ও সংগীতের জয়গান। প্রতি বছর এই দিনে সংগীতপ্রেমীরা নানা আয়োজনে উদযাপন করেন বিশ্ব সঙ্গীত দিবস বা ফেট দ্য লা মিউজিক (Fête de la Musique)। সঙ্গীতকে মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তুলে ধরতে ১৯৮২ সালে ফ্রান্সে প্রথম এই দিবসটির সূচনা হয়। পরবর্তীতে এটি বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে এক আনন্দঘন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।
কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আজ সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক চেতনার অবস্থান এক জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি।
বাংলাদেশি জাতি গান-নাচে অনুরক্ত, বলা চলে, ‘নাচ-গান পাগল’। আবার এই জাতি স্বাধীনতাপ্রিয়, স্বেচ্ছাচারিতার স্বাদ নিতেও অভ্যস্ত। অথচ এই স্বাধীনতা অনেক সময় দায়িত্বহীনতায় রূপ নেয়, যে আচরণ বিশ্বের বহু দেশে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। রুশোর 'মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্ম নেয়'- এই বাণীর খণ্ডাংশ যেনো বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আত্মঘোষিত নীতি, অথচ তার পরবর্তী অংশ- 'তবে সর্বত্র সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ' কথাটি তাদের অভিধানে নেই। এখানেই সাংস্কৃতিক দ্বৈততা ও আত্মপ্রবঞ্চনার সূচনা।
বাংলাদেশে ‘কাগজ’ বহনের স্বাধীনতা যেমন আছে, তেমনি ‘কাগজ যাচাইয়ের’ ক্ষমতা আছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে। একদিকে ভূয়া সনদ, পরিচয়পত্র, লাইসেন্স ইত্যাদি, অন্যদিকে সেগুলো বৈধ বা অবৈধ ঘোষণার চূড়ান্ত ক্ষমতা- এই দুই শক্তির টানাপোড়েনে রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা এবং সংস্কৃতি বিপন্ন।
দিনের শুরু হয় শপথ দিয়ে, কিন্তু শেষ হয় গানে। কেউ গুনগুন করে, কেউ শিস দিয়ে, কেউবা 'নিনি...নি…' বলে নিজের মতো গায়। এদেশের নাচগান একদিকে যেমন সর্বজনীন আনন্দ, অন্যদিকে কখনো কখনো চূড়ান্ত আত্মবিসর্জনের উদাহরণও। গান নিয়ে মানুষ হাসে, কাঁদে, প্রেমে পড়ে, এমনকি খুনও করে।
বাংলাদেশে কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি ঘোষণা করা হলেও ২০২৪ সাল পর্যন্ত তা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়নি। এর পেছনে রাজনীতি, রাষ্ট্রচিন্তা এবং সাংস্কৃতিক কূটকৌশলের মিলিত প্রভাব কাজ করেছে। জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম- এই দুই ব্যক্তিকে সাংবিধানিক কাঠামোতে একত্রে স্বীকৃতি দিতে গেলে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে- এমন ধারণা নিয়েই এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব।
এটি আমাদের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের দুর্বলতার এক করুণ প্রতিচ্ছবি। আমরা যতবার সংগীত দিবস উদযাপন করি, ততবারই এই সাংগঠনিক ও সাংবিধানিক অসংগতি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয় যে,আমাদের সঙ্গীতচর্চা ও সাংস্কৃতিক নীতিনির্ধারণ কতটা তাল-বেতাল ও ছন্দহীন।
সঙ্গীতের তাৎপর্য কেবল রম্যতা বা ফুর্তি নয়। প্রাচীন দার্শনিক পীথাগোরাস থেকে শুরু করে প্লেটো, সক্রেটিস, এবং আধুনিক যুগের আইনস্টাইন, চে গুয়েভারা, নজরুল, করিম শাহ, সলিল চৌধুরী কিংবা ভূপেন হাজারিকা সবাই বিশ্বাস করতেন- সঙ্গীত মানুষের নৈতিকতা, শিক্ষা, সচেতনতা ও প্রতিবাদের অনন্য ভাষা।
গান হয়ে উঠতে পারে প্রতিবাদের হাতিয়ার, জীবন বদলের অনুপ্রেরণা, সমাজ পরিবর্তনের মন্ত্র। কিন্তু যখন গান হয়ে ওঠে শুধুই পণ্যের মতো বিক্রয়যোগ্য, তখন তার প্রাণ হারায়। বাংলাদেশে যেমন দেখা যায়- একদিকে 'শোন একটি মুজিবর থেকে' কিংবা 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম'-এর মতো আত্মস্মরণমূলক গান, অন্যদিকে 'ফাইট্টা যায় বুকটা' বা 'ও টুনির মা'-এর মতো বাজারধর্মী গান- সমান জনপ্রিয়। গান হয়ে গেছে পণ্যের মতো, যার ভোক্তাপ্রিয়তা যত, তার 'মূল্য' তত।
বালাদেশের শহরে-গঞ্জে-গ্রামে-মহল্লায় প্রতিবছর দুইবার করে মহান কবি-শিল্পী-গায়কের জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন ও শতশত গান করা হয়ে থাকে। প্রায় সবখানেই, গীত হওয়া গানের কবি-গীতিকার-সুরকার কে বা কারা সে নামটিও উচ্চারণ করতে শুনা যায় না। ফলে, কিছুই শেখা হয় না। শব্দযন্ত্রের তীব্রতা ও বাদ্যযন্ত্রের বিকট আওয়াজ তথা ডিজে বিনোদনের নামে পরিবেশ দূষণ করে চলেছে। শিক্ষা ও আদর্শশূন্য সমাজে সঙ্গীত হয়ে উঠেছে কেবল বাহ্যিক চটক, ভেতরে ফাঁপা। অজ্ঞতা, অবহেলা ও সংস্কৃতির অপব্যবহার আজ সঙ্গীতকে জীবনবিমুখ এক আয়োজন করে তুলেছে।
বিশ্ব সঙ্গীত দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়- গান শুধু কণ্ঠের নয়, মন ও মস্তিষ্কের বিষয়। গান হোক হৃদয়ের কথা, সমাজের দর্পণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। গান হোক আলোর মতো, যা পথ দেখায়, নয় কেবল উল্লাসের ধোঁয়া।
বাংলাদেশ যদি সত্যিকার অর্থে সাংস্কৃতিক জাতি হতে চায়, তবে গানকে শুধু বাজারের পণ্য নয়, শিক্ষা, সচেতনতা ও জীবনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কেবল তখনই সঙ্গীত দিবস হয়ে উঠবে- জাতির আত্মজাগরণের প্রতীক।