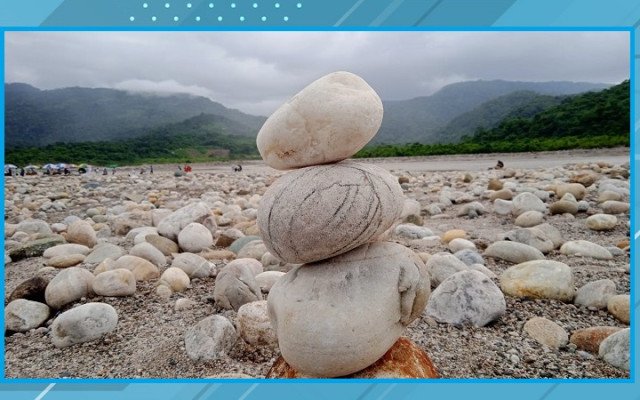
ছবি: সংগৃহিত।
বাংলাদেশের সিলেট সীমান্তে যে সাদা পাথর পাওয়া যায়, তার মূল উৎস ভারতের মেঘালয় মালভূমি। এ মালভূমি গ্রানাইট ও নাইসের মতো শক্ত শিলা দিয়ে গঠিত।
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বৃষ্টি, তাপমাত্রার পরিবর্তন ও বাতাসের কারণে এই শিলাগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। ক্ষয়ের ফলে কোয়ার্টজসহ শক্ত খনিজ ভেঙে নুড়ি ও পাথরে রূপ নেয়।
বর্ষাকালে পাহাড়ি ঢল নামলে খরস্রোতা নদীগুলো- যেমন পিয়াইন, ধলাই ও গোয়াইন হয়ে এসব নুড়ি ও পাথর স্রোতের সঙ্গে বাংলাদেশে নিয়ে আসে। যখন নদী খাড়া পাহাড়ি ঢাল বেয়ে সমতলে নামে, তখন প্রবল স্রোতের গতি কমে যায় এবং ভারী পাথরগুলো নদীর বাঁকে বা চরে জমে ওঠে।
ফলে ভোলাগঞ্জ, জাফলং, বিছানাকান্দি ও লোভাছড়ার মতো স্থানে প্রাকৃতিকভাবে বিপুল পরিমাণ পাথর সঞ্চিত হয়। ভূতত্ত্বে এ ধরনের সঞ্চয়নকে বলা হয় প্লাসার ডিপোজিট বা প্রাকৃতিক সঞ্চয়। একে এলুভিয়াল ডিপোজিটও বলে, যা নদী বা স্রোতবাহিত পলি, বালি, মাটি ও অন্যান্য পদার্থ যা পানিতে ভেসে এসে স্রোতের গতি কমে গেলে বা থেমে গেলে জমা হয়।
খনির প্রকৃতি: এগুলো ভূগর্ভস্থ খনি নয়, বরং উন্মুক্ত বা সারফেস ডিপোজিট। পাথর সরাসরি নদীর চর ও তলদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়।
নবায়নযোগ্য সম্পদ: প্রতি বর্ষায় নতুন পাথর ভেসে এসে জমা হয়। তাই এটি একধরনের নবায়নযোগ্য ভান্ডার।
সম্পদ পরিমাণ: নির্দিষ্ট পরিমাণ বলা কঠিন। তবে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের (জিএসবি) এক জরিপ অনুযায়ী শুধু ভোলাগঞ্জেই প্রায় ১০.৬ কোটি ঘনফুট পাথরের মজুদ অনুমান করা হয়েছিল।
জরিপ অনুযায়ী পাথরের সবচেয়ে বড় মজুদ ভোলাগঞ্জে। আর ক্ষুদ্র মজুদ জাফলং, বিছানাকান্দি, লোভাছড়ায়।
তবে অনেকের মতে, বিছানাকান্দিতেও ভোলাগঞ্জের তুলনায় বেশি পাথর মজুদ রয়েছে।
মেঘালয়ে খনি, বাংলাদেশে সঞ্চয়ন
মেঘালয়ে মূল চুনাপাথরের স্তর থাকে পাহাড়ের ভেতরে। সেখানকার কোম্পানিগুলো (যেমন Lafarge, Komorrah) সরাসরি খনি খুঁড়ে পাথর উত্তোলন করে।
মেঘালয়ের পাহাড় থেকে পাথর স্বাভাবিকভাবে নদীপথে নেমে এসে বাংলাদেশের সিলেট সীমান্তে জমা হয়। বাংলাদেশে পাথর তুলতে আলাদা খনি খননের দরকার পড়ে না, যেন প্রকৃতি নিজে ডেলিভারি দিয়ে দেয়।
অর্থনৈতিক গুরুত্ব
এই সাদা পাথর ভবন, সেতু, সড়ক, কালভার্ট নির্মাণে অপরিহার্য কাঁচামাল।
সিলেট অঞ্চলের হাজার হাজার শ্রমিকের জীবিকা নির্ভর করে পাথর উত্তোলন, ভাঙা ও পরিবহনের ওপর।
পরিবেশগত সংকট ও নিষেধাজ্ঞা
অপরিকল্পিতভাবে অতিরিক্ত পাথর উত্তোলনের ফলে- নদীর তীর ভাঙন, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, জলজ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি ইত্য়াদি সমস্যা দেখা দেয়।
২০১৮ সালে পরিবেশবাদীদের রিটের প্রেক্ষিতে ভোলাগঞ্জ-জাফলংসহ পুরো সিলেট অঞ্চলের কোয়ারিগুলোকে ‘পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা’ ঘোষণা করে সরকার। ফলে ২০১৮ থেকে ২০২৫ পর্যস্ত দীর্ঘ সাত বছর পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে।
যদিও এ সময়ে স্থানীয় হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে, অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। পরে ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ সালে সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। তবে পরিবেশবাদীরা এ সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
নিষেধাজ্ঞা ও বন্যার সম্পর্ক:
২০১৮ সালে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পরপরই সিলেটে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। এরপর ২০১৯, ২০২০, ২০২২ এবং ২০২৪ সালেও বড় বন্যা হয়।
অনেকে মনে করেন, পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকায় নদীর প্রবাহ ও পলি জমায় প্রভাব ফেলেছিল।
তবে বিশ্লেষণে দেখা যায়— বন্যার মূল কারণ ছিল অতিবৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা অতিরিক্ত পানি এবং নদীর ধারণক্ষমতা হ্রাস।
সীমান্তপারের বৈপরীত্য
যখন বাংলাদেশে সাত বছর ধরে কোয়ারি বন্ধ ছিল, তখন সীমান্তের ওপাশে মেঘালয়ে শত শত কোয়ারি চালু ছিল। সেখানে পাহাড় কেটে বিপুল পরিমাণ পাথর সংগ্রহ করা হয়েছে।
ফলে বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া সম্পদ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।
অবাধে পাথর উত্তোলনের ফলে নদীর ভাঙন, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, ধুলো-দূষণ এবং স্থানীয় মানুষের জনজীবন ব্যাহত হওয়ার মতো সমস্যা থেকে রেহাই পেতে করণীয় হিসেবে সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলনের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, যান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে সনাতনী পদ্ধতি ব্যবহার, পর্যটন অঞ্চলগুলোকে সুরক্ষা প্রদান এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প উপকরণ ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।
তথ্য সংগ্রহ: মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম।











